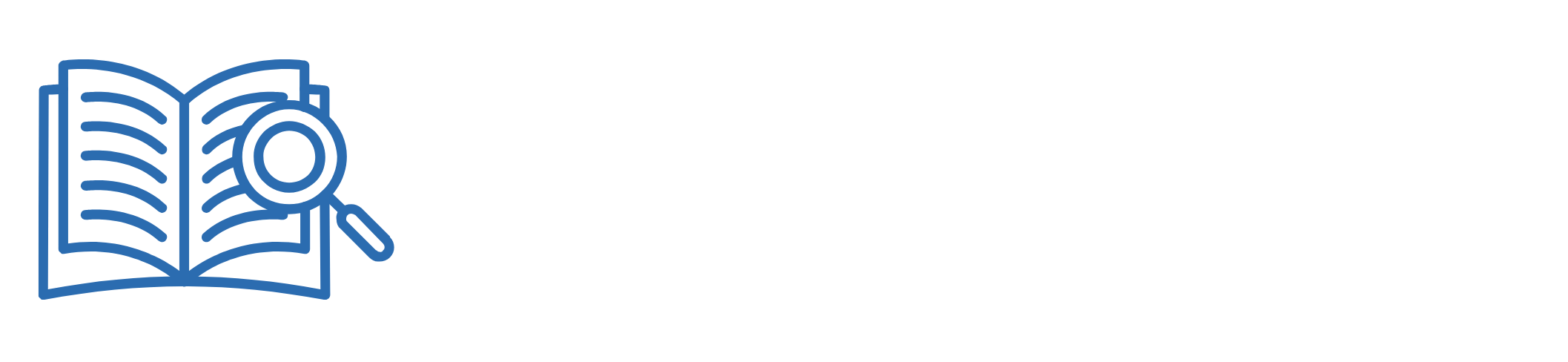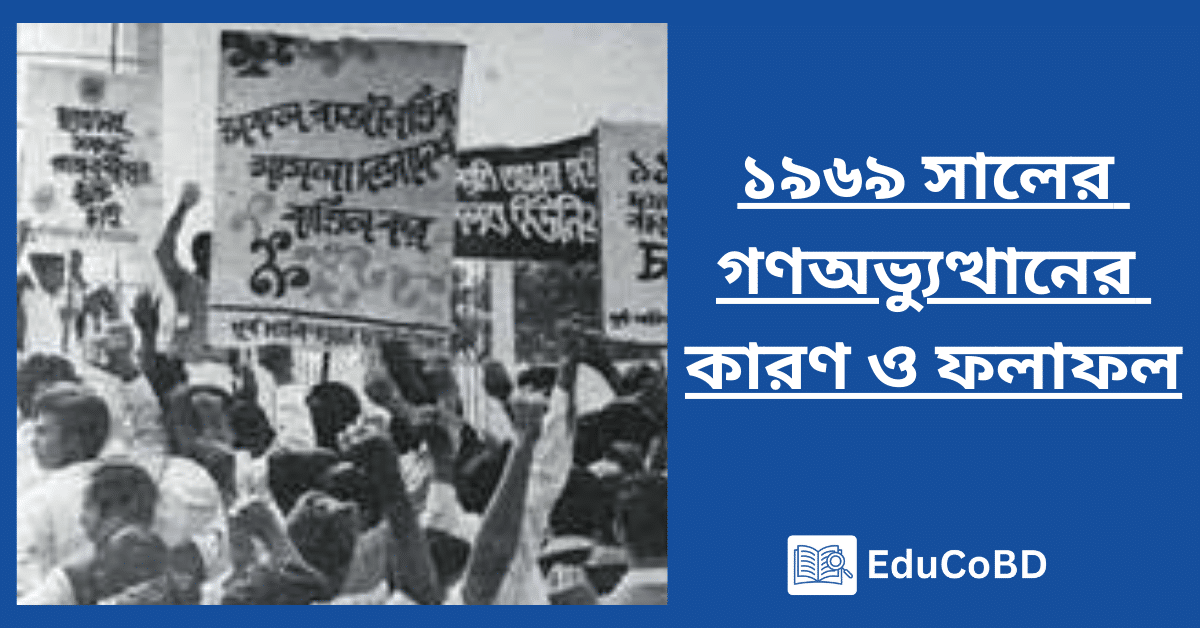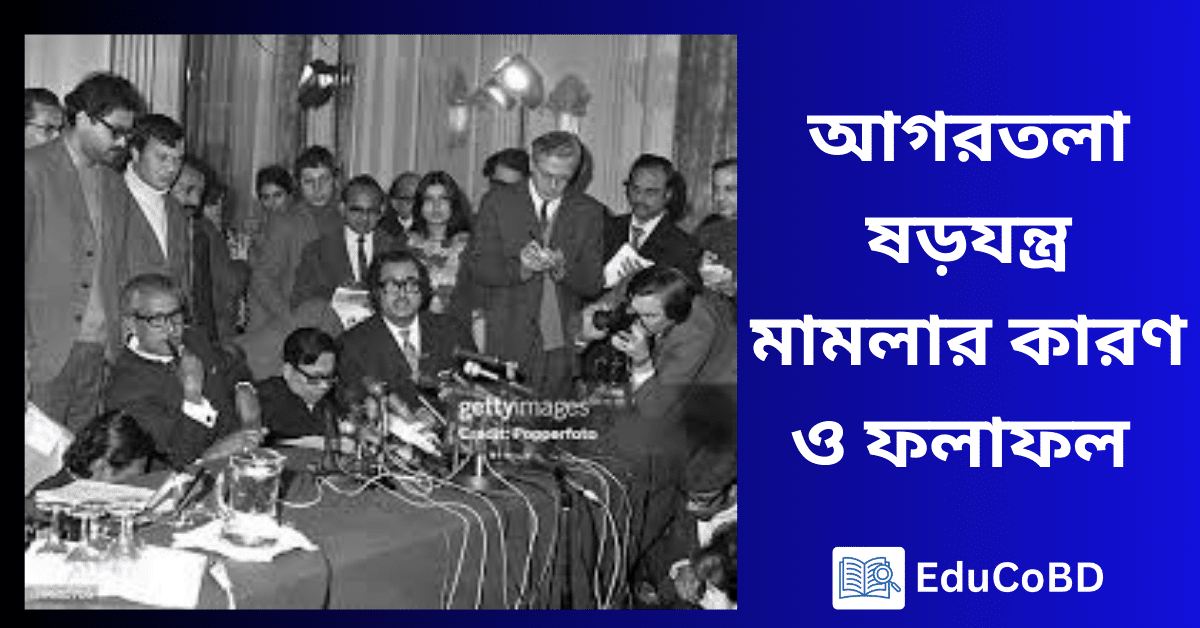বঙ্গভঙ্গের কারণ ও ফলাফল সহ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস
বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গভীর প্রভাব বিস্তরণশীল ঘটনা ছিলো ১৯০৫ সালে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠন। ১৯০৫ সালে ঢাকা কেন্দ্রিক নতুন প্রদেশ গঠন উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি ক্রান্তিকালীন অধ্যায়রূপে ভারতীয় রাজনীতিতে সৃষ্টি করে এক বড় ধরনের অভিধান। ইংরেজ শাসকগন তাদের প্রশাসনিক প্রয়োজনে বিশাল বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সি ভাগ করেন। এটিকে তারা দেখেছেন একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তরূপে। আর পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানগন ঢাকা কেন্দ্রিক নতুন প্রদেশকে দেখেছেন তাদের ভাগ্য উদয়ের প্রথম প্রভাত রূপে। অন্যদিকে কলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণ হিন্দু , জমিদার, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগন এ ঘটনাকে মূল্যায়ন করেছেন দেড়শতাধিক বছরকালে গড়ে তোলা তাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পিতৃভূমির ওপর আঘাতরূপে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলেও এর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে।
বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপট বা পটভূমিঃ
বঙ্গভঙ্গের পূর্বে বাংলা প্রেসিডেন্সি বৃটিশ ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রদেশ ছিল। বাংলা, বিহার, ওড়িষ্যা ও আসাম নিয়ে এ প্রদেশ গঠিত ছিল। এর শাসনভার ন্যস্ত ছিল একজন গভর্ণর বা ছোট লাটের ওপর। বঙ্গভঙ্গের পটভূমি হিসেবে প্রথমে আলোচনা করব পৃথক প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব ও বঙ্গভঙ্গের প্রাথমিক পদক্ষেপ যা ১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত হয়েছিল।
১৮৫৩ সালে স্যার চার্লস গ্র্যান্ট শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করার প্রস্তাব করেন। ১৮৫৪ সালে লর্ড ডালহৌসি বাংলা ভাগ না করে বাংলা, বিহার, ওড়িষ্যা ও আসামে বাংলা প্রেসিডেন্সি গঠন করেন। ১৮৬৬ সালে ওড়িষ্যাতে চরম দূর্ভিক্ষ দেখা দিলে কলকাতা কেন্দ্রিক প্রশাসন সেখানে সহজে ত্রান সামগ্রী পেীছাতে ও বন্টন করতে ব্যর্থ হন। ভারত সচিব স্যার স্টাফোর্ড হেনরি নর্থকোট ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে এ দূর্ভিক্ষের কারন অনুসন্ধান করতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তদন্ত কমিটি সুপারিশ করেন যে, প্রদেশের বিশালায়তন দূর্ভিক্ষ ও দূর্ভিক্ষ মোকাবেলায় সরকারের ব্যর্থতার অন্যতম কারন। তদন্ত কমিটি বাংলা প্রদেশ বিভক্তির সুপারিশ করেন। বাংলার ছোট লার্ট স্যার উইলিয়াম গ্রে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে এবং স্যার জন ক্যাম্বেল ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ঊর্ধ্বতন কতৃপক্ষের নিকট লিখিত অভিযোগ করেন যে, বাংলার মতো বিশালায়তন প্রদেশ এর শাসন পরিচালনা একজন গভর্ণরের পক্ষে সম্ভব নয়। তারাও বাংলা প্রদেশ বিভক্তির সুপারিশ করেন।
২৯ আগস্ট ১৮৭৪ এ বাংলা প্রেসিডেন্সি হতে আসামকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং আসামের প্রশাসন একজন কমিশনারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। সিলেট, কাছার প্রভৃতি বাংলা ভাষাভাষি জেলাগুলো আসামের অধিভূক্ত করা হয়। এই হলো ইংরেজ সরকারের বঙ্গভঙ্গের প্রথম পদক্ষেপ।

কিন্তু এতেও প্রশাসনিক সমস্যার সুরাহা হয় নি।
১৮৯৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর লর্ড কার্জন ভারতের বড় লার্ট হিসেবে নিযুক্ত হন। এদিকে মধ্য প্রদেশের চীফ কমিশনার এন্ড্রু ফ্রেজার ১৯০১ সালে ওড়িশ্যাকে বাংলা প্রদেশ থেকে আলাদা করে মধ্য প্রদেশের সাথে যুক্ত করার প্রস্তাব করেন। পরবর্তীকালে এন্ড্রু ফ্রেজার বেঙ্গল প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্ণর নিযুক্ত হন। দায়িত্ব প্রাপ্তির অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এন্ড্রু ফ্রেজার বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা লর্ড কার্জনের নিকট পেশ করেন। লর্ড কার্জনও বঙ্গভঙ্গের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন।
রিজলে নোটঃ
লর্ড কার্জন ১৯০২ সালে বাংলা প্রদেশের সীমানা পুনঃনির্ধারনের জন্য বৃটিশ সরকারকে অনুরোধ করেন। লর্ড কার্জনের অনুরোধ মোতাবেক বৃটিশ সরকার ভারত সরকারের সচিব হারবার্ট হোপ রিজলে (Herbert Hope Risley) এর নেতৃত্বে বাংলার সীমানা নির্ধারন কমিটি গঠন করা হয়। হারবার্ট রিজলে ঢাকা, চট্রগ্রাম ও ময়মনসিংহ কে আসামের সাথে সংযুক্ত করে চীফ কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত করার প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবটি রিজলে নোট বা রিজলে প্রস্তাব নামে পরিচিত।
বড়লাট কার্জন বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলা অঞ্চল পরিদর্শনে আসেন। ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহ লর্ড কার্জনকে রাজকীয় আতিথিয়তা প্রদান করেন। নবাব সলিমুল্লাহ পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে একটি পৃথক প্রদেশ গঠনের দাবি জানান। লর্ড কার্জন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনা ভারত সচিব রডারিকের নিকট ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রেরন করেন।

বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা বা বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা বাস্তবায়নঃ
ভারত সচিব রডারিক বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। ১৯০৫ সালের ১০ জুলাই এ পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। ফলে পূর্ববাংলা ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। নতুন প্রদেশের শাসনভারের দায়িত্বে থাকবেন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর বা ছোট লার্ট। ঢাকা নতুন প্রদেশের রাজধানী এবং চট্রগ্রাম বিকল্প রাজধানী নির্বাচিত হয়। তবে নতুন প্রদেশের বিচার বিভাগ কলকাতা হােইকোর্টের অধীনে রাখা হয়। স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার নতুন প্রদেশের গভর্ণর বা ছোট লার্ট নির্বাচিত হয়।
নতুন প্রদেশ অর্থাৎ পূর্ববাংলা ও আসামের আয়তন ও জনসংখ্যাঃ
আয়তন: ১০৬,৫০৪ বর্গমাইল।
জনসংখ্যা: ৩,১০,০০,০০০।
মুসলমান: ১,৮০,০০০০০।
হিন্দু: ১,২০,০০,০০০। অবশিষ্ট বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী।
বাংলা তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের আয়তন ও জনসংখ্যাঃ
প্রাক্তন বাংলা প্রেসিডেন্সির অবশিষ্টাংশ পশ্চিম বাংলা, বিহার ও ওড়িশ্যা নিয়ে গঠিত বাংলা প্রদেশ। এটি পশ্চিম বাংলা নামে সমধিক পরিচিত হয়ে ওঠে।
এ প্রদেশের রাজধানী হয় কলকাতা।
প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্ণর নিযুক্ত হয় অ্যান্ড্রু ফ্রেজার।
এ প্রদেশের আয়তন ছিল ১,৪১,৫৮০ বর্গমাইল
জনসংখ্যা ছিল ৫,৪০,০০,০০০ তার মধ্যে হিন্দু ৪,২০,০০,০০০ জন, মুসলমান ৯০,০০,০০০ জন, অবশিষ্ট অন্যান্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভু্ক্ত ছিল।
হিন্দুদের প্রবল বাঁধা ও প্রতিবাদ স্বত্ত্বেও ভারত সচিবের অনুমতি নিয়ে এ বিভক্তি ১৯০৫ সালের ৬ অক্টোবর কার্যকর হয়।
বঙ্গভঙ্গের পেছনে কারণঃ
প্রশাসনিক কারণঃ
১৭৬৫ সাল থেকে বাংলা, বিহার, ওড়িশ্যা নিয়ে গঠিত বাংলা বৃটিশ ভারতের সর্বাপেক্ষা বড় প্রদেশ। লর্ড কার্জনের সময় এর আয়তন ছিল ১,৮৯,০০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি ৮০ লক্ষ। একজন গভর্ণরের পক্ষে এ বিশাল আয়তন প্রদেশের বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যাকে শাসন করা দুরূহ হয়ে পড়েছিল। কেননা নদ-নদী ও খাড়ি সমূহ দ্বারা অত্যধিক বিচ্ছিন্ন পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পুলিশী কাজ চালানো অসুবিধাজনক ছিল। জলপথে সংঘবদ্ধ জলদস্যুতা অন্তত এক শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সুতরাং প্রশাসনিক অসুবিধা দূরীকরনের লক্ষ্যে বাংলাকে ভাগ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

রাজনৈতিক কারনঃ
প্রশাসনিক উদ্দেশ্য থাকলেও শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গের পেছনে রাজনৈতিক কারনও বিদ্যমান ছিল। সুমিত সরকার, অমলেশ ত্রিপাঠি, ড. এমাজুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ মনে করেন যে, বঙ্গভঙ্গের পেছনে রাজনৈতিক কারনই ছিল মূখ্য।
হিন্দু মুসলমান বিভেদ সৃষ্টি অর্থাৎ ডিভাইড এন্ড রুল পলিসিঃ
বৃটিশদের ইচ্ছা ছিল স্থায়ীভাবে ভারতে শাসন প্রতিষ্ঠা করা। তাই তারা স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভাগ কর ও শাসন কর অর্থাৎ ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি (Devide and Rule) প্রবর্তন করেন। এ নীতি অনুসারে বৃটিশরা ভারতবর্ষে প্রধান দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে প্রচেষ্টা চালায়। বৃটিশ সরকার প্রথম দিকে ভারতবর্ষের হিন্দু সম্প্রদায়কে পৃষ্ঠপোষকতা দান করে। বাংলার হিন্দু জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি, প্রশাসনিক পদে হিন্দুদের একচেটিয়া নিয়োগ দান, শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাধিক সুযোগ দান, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের অপ্রতিরোধ্য এসব কিছুর মাধ্যমে বাঙ্গালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভিারতের রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থান সুসহত করে। এভাবে বৃটিশ সরকার ভারতে মুসলমানেদেরকে হিন্দু বিদ্বেষী করে তোলে। তাই বৃটিশ সরকার চেয়েছিলো বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্রুত বধনশীলতাকে ব্যাহত করা এবং পূর্ব বাংলায় মুসলিম প্রভাব বাড়ানোকে উৎসাহিত করা।
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গতি স্থিমিত করাঃ
বৃটিশরা গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলেন যে, বাঙালী মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীরা ভারতে জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্মদাতা। ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের ফলে ভারতবর্ষে বাঙ্গালিরা রাজনৈতিভাবে সচেতন হয়। তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটে। ভারতবর্ষকে বৃটিশদের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার জন্য ১৯০০ সালে ঢাকায় অনুশীলন সমিতি এবং ১৯০১ সালে কলকাতায় যুগান্তর নামে দুটি বিপ্লবী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই বৃটিশরা বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করে তাদের শাসনকে দীর্ঘায়িত করার কৌশল গ্রহণ করে।
অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণঃ
বঙ্গভঙ্গের পেছনে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারন অর্থনীতি। কলকাতা ছিল তৎকালীন বৃটিশ ভারতের রাজধানী। তাই সে সময়ের বাংলার শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কলকাতাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। বৃটিশ শাসনে এদেশে যা কিছু উন্নয়ন ও কল্যানমূলক কাজ হয়েছিল তা ছিল রাজধানী কলকাতাকে ঘিরে। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে একমাত্র কলকাতাতেই ২২টি কলেজ ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। পাশাপাশি এ সময় পূর্ব বাংলাতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। তাই পূব বাংলার জনগন শিক্ষার দিক থেকে পশ্চাৎপদ ছিল। বঙ্গভঙ্গের ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ বাঙ্গালী মুসলমান উন্নতি করবে বলে লর্ড কার্জন মনে করেন।
তাছাড়া পূর্ববঙ্গের অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক। এখানকার কৃষকশ্রেণী ছিল অধিকাংশ মুসলমান। তারা ছিল হতদরিদ্র, অর্থনৈতিকভাবে পর্যদুস্ত। কলকাতাকেন্দ্রীক বুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেনীর হাতে তাদের জীবনযাত্রা নির্ভর করতো। পূর্ব বাংলার জমিদরশ্রেনী এখানকার অর্থে কলকাতায় বিলাস ব্যসনে মত্ত থাকতো। সমগ্র পূর্ববঙ্গ ছিল কলকাতার শিল্পের কাঁচামালের সরবরাহকারী এবং কারখানায় উৎপাদিত পন্যের বাজার।
অধিকন্তু পূর্ববঙ্গের প্রধান অর্থকরী ফসল ছিল পাট যা সোনালি সূর্য নামে জগদ্বিখ্যাত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলার অধিকাংশ কারখানা এবং পাটকলগুলো স্থাপিত হয়েছিলো কলকাতার আশেপাশে হুগলি নদীর তীরে। এর ফলে বেকারত্ব পূর্ববাংলার অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। তাই লর্ড কার্জন প্রশাসনিক বৈষম্য দূর করা ছাড়াও অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যাতে পূর্ববাংলা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে বঙ্গভঙ্গের চিন্তা করে।
১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গে হিন্দুদের বিরোধিতার কারনঃ
(১) হিন্দু জমিদার ও বুদ্ধিজীবীদের বিরোধিতাঃ
বঙ্গভঙ্গ হিন্দু জনগনের মনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে। কারন বঙ্গভঙ্গের পূর্বে হিন্দুরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বহুবিধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছিলো। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নয়নের ব্যাপক সম্ভাবনা দেখা দেয়। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার নিপীড়িত মুসলমান সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা উজ্জীবিত হবে। ফলে হিন্দু জমিদার ও বুদ্ধিজীবীরা মুসলমানদের ওপর তাদের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব হারাবে।
(২) হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতাদের বিরোধিতাঃ
হিন্দুদের জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা এ সময় ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করছিলো। হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতাগন এরূপ ব্যাখ্যা দিতে থাকেন যে, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসরমান হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক বিকাশকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার পূর্ব বাংলার বাঙ্গালি মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের এটি ছিল প্রধান কারন।
(৩) শিল্পপতি ও পুঁজপতিদের বিরোধিতাঃ
ঢাকায় নতুন প্রদেশের রাজধানী স্থাপিত হলে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। অপরদিকে কলকাতার সমৃদ্ধি ক্রমশ হ্রাস পাবে। সেখানে পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের একচেটিয়া ব্যবসার বিঘ্ন ঘটবে। ব্যবসায়িক স্বার্থ বিঘ্ন হবার আশঙ্কায় হিন্দু ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা নতুন প্রদেশ গঠনের বিরোধিতা করেছিলো।
(৪) আইনজীবীদের বিরোধিতাঃ
আইনজীবীগন মনে করলেন যে, ঢাকায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের আইন ব্যবসায় ভাটা পড়তে পারে কারন অধিকাংশ মক্কেলই ছিল পূর্ববঙ্গের।
ঐতিহাসিক H.H Dodwell তাঁর The Cambridge History of India গ্রন্থে বলেন, কলকাতার আইনজীবীরা ভীত হয়েছিল এই কারনে যে, নতুন প্রদেশ গঠিত হলে ঢাকায় আপীল কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হবে।
(৫) সংবাদপত্র মালিকদের বিরোধিতাঃ
কলকাতার সংবাদপত্রের মালিকরা মনে করলেন, নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে সংবাদপত্র প্রকাশিত হবে এবং সেক্ষেত্রে তাদের সংবাদপত্রের চাহিদা বহুলাংশে কমে যাবে। কারন পূর্ব বাংলার পাঠকগন সংবাদের জন্য ঢাকার প্রতি তাকিয়ে থাকবে স্বাভাবিকভাবেই।
এ সকল কারনের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার সাংবাদিক,আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনী নিজেদের শ্রেনীগত স্বার্থ ও প্রাধান্য বজায় রাখার জন্যই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন।
এই আন্দোলনের প্রানকেন্দ্র ছিল কলকাতা। অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন চন্দ্র পাল, অশ্বিনী কুমার দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বালাগঙ্গাধর তীলক এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। কাশিমবাজারের মহারাজা মহেন্দ্র চন্দ্রনন্দী ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউনহলে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভায় বলেন, নতুন প্রদেশে মুসলমানরা হবে সংখ্যাগুরু আর বাঙ্গালি হিন্দুরা হবে সংখ্যালঘু। ফলে স্বদেশেই আমরা হবো পরবাসী। আমাদের জাতীর ভাগ্যে ভবিষ্যৎ কি হবে তা চিন্তা করে আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি।
বিমলানন্দ শাসমল তাঁর ‘ভারত কী করে ভাগ হলো নামক গ্রন্থে তিনি ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ব বাংলা ও আসাম নতুন প্রদেশ গটনের বিরুদ্ধে কলকাতাকেন্দ্রীক হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া অল্প কথায় সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।
মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর India wings freedom গ্রন্থে লিখেছেন, বিপ্লবীরা যে শ্রেণী থেকেই আসুক না কেন প্রত্যেকেই ছিলেন মুসলিম বিরোধী
হিন্দু সমাজের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনঃ
কংগ্রেসের প্রচারণা ও বয়কট আন্দোলনঃ
কংগ্রেস নেতাগণ প্রচার করতে থাকেন যে, সাংগঠনিকভাবে তাদেরকে এবং হিন্দু সম্প্রদায়কে দুর্বল করে ফেলার জন্য অর্থাৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার আগেই এ পরিকল্পনা বাতিলের দাবিতে ১৯০৫ সালের ১৭ জুলাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস খুলনার বাগেরহাটে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বৃটিশদের বিরুদ্ধে বয়কট প্রস্তাব গ্রহণ করে। এ প্রস্তাবে বলা হয়, যতদিন পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ রদ না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত বৃটিশ পণ্য সামগ্রী বয়কট করা হবে।
পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারণাঃ
১৯০৫ সালের ৭ জুলাই হিতবাদী পত্রিকায় বলা হয় বিগত ১৫০ বছরের মধ্যে বাঙ্গালি জাতীর সম্মুখে এরূপ বিপর্যয় আর কখনো আসে নাই। ১৯০৫ সালের ১৩ জুলাই কৃঞ্চকুমার মিত্র সম্পাদিত সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিলাতি পণ্য বর্জনের পক্ষে ঘোষণা করা হয়।
১৯০৫ সালের ১৮ই জুলাই সন্ধ্যা প্রত্রিকায় বলা হয়, বাঙ্গালি জাতীকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাগন পত্র-পত্রিকায় বক্তৃতা মঞ্চে একে বাঙ্গালি বিরোধী, জাতীয়তাবাদী বিরোধী এবং বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি বিশেষনে আখ্যায়িত করে। সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার পরদিনই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে ভুপেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি কর্তৃক বেঙ্গলি পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গকে এক গুরুতর জাতীয় বিপর্যয় বলে মন্তব্য করা হয় এবং সরকারকে ভারতব্যাপী এক জাতীয় সংগ্রামের জন্য সতর্ক করে দেয়া হয়। ১৯০৫ সালের ১৭ ও ১৮ জুলাই কলকাতার রিপন কলেজে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এক বিপ্লবী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউনহলে ছাত্ররা নতুন করে বিলেতি পণ্য বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলনের জন্য নতুন করে শপথ করে। বিলেতি সামগ্রী বস্ত্র, লবন, চিনি প্রভৃতি কোন পূজা-পার্বণে ব্যবহার করলে পুরোহিতরা পূজা করতে অসম্মত হয়। এভাবে ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নিচু সকলেই বয়কট আন্দোলনে যোগদান করলে সে আন্দোলন এক শক্তিশালী বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে পরিনত হয়। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, বঙ্গভঙ্গের ফলেই ভারতে প্রকৃত নবজাগরণ ঘটেছে।
বয়কট আন্দোলনের ইতিবাচক দিকঃ
বয়কট আন্দোলন ছিল নেতিবাচক আন্দোলন বলা যেতে পারে। এ আন্দোলন বৃটিশ জাতীর স্বার্থের ওপর কঠোর আঘাত হেনেছিল সন্দেহ নেই। বয়কট আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষে নিজস্ব পণ্য উৎপাদন শুরু হয়। স্বদেশী শিল্পজাত সামগ্রী ব্যবহার বৃটিশকে কঠোর আঘাত হানে বিলেতি পণ্যের বিপরীতে দেশী মৃত বা মৃতপ্রায় শিল্পগুলোকে পুনর্জাগরন করা হয়। বিলেতি পণ্য বর্জনের মাধ্যমে বৃটিশদের অর্থনৈতিক চাপে ফেলা এবং বঙ্গভঙ্গ রদ করাই ছিল বয়কট আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য।
কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রচারণাঃ
১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার দিন ঠিক হয়। কংগ্রেস সেদিন দেশব্যাপী শোক দিবস পালন করে। অমরেন্দ্রনাথ সেদিন দেশব্যাপী ভাতৃত্বের প্রতীক রাখি সংক্রান্তি উৎসব উদযাপন করে। অবিবেচ্ছদের প্রতীক হিসেবে হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান নির্বিশেষে একে অপরের হাতে রাখি বেঁধে দেন। শোক প্রকাশের চিহ্ন স্বরূপ সকলে উপবাস করে। দোকনপাট ও অন্যান্য কাজকর্ম বন্ধ রাখে। হিন্দদের মধ্যে উগ্র জাতীয়তবাদ জগরনই ছিল এসব কর্মসূচীর উদ্দেশ্য।
কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমাচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি রচিত স্বদেশী গান বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আমার সোনার বাংলা গানটি বঙ্গভঙ্গকে নিরুৎসাহিৎ করার উদ্দেশ্যে রচনা করেন। স্বদেশ বন্দনার নামে বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলিম বিদ্বেষীমূলক ‘বন্দে মাতরম’ কে জাতীয় সংগীতরূপে চালু করে।
তাছাড়া কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীরা প্রচার করতে থাকেন যে, বঙ্গভঙ্গ হচ্ছে বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ এবং এটা দেবী কালীর প্রতি অপমানজনক। বরিশালের চারণ কবি মুকুন্দ দাস গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে দেশপ্রেম জাগাতে সক্ষম হন।
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনঃ
বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলা তথা ভারতবর্ষে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তা ধীরে ধীরে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে রূপ নেয়। উগ্র জাতীয়তাবাদীরা মনে করতে থাকে যে, স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সারা ভারতে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ দানা বাঁধতে থাকে। এদের মধ্যে কলকাতার অনুশীলন ও ঢাকার যুগান্তর অন্যতম। ঢাকায় অনুশীলন সমিতির প্রধান নেতা ছিলেন পুলিন বিহারী দাস। চিত্তরঞ্জন দাস এই অনুশীলন ও যুগান্তরের পেছনে বহু অর্থ ব্যয় করেন। বারীন্দ্র কুমার ঘোষ যুগান্তর পার্টির প্রধান ছিলেন।
এদিকে কলকাতায় লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড দেয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। ক্ষুধিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি নামে দুই বিপ্লবী বিহারের মোজাফফরপুরে কিংসফোর্ডের গাড়ির ওপর বোমা নিক্ষেপ করে। এতে ক্ষুধিরামবসুর ফাঁসি হয়।
স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর নীতিঃ
স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে মূলত ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু বৃটিশ সরকারের প্রচন্ড দমন নীতির ফলে বিশেষত বালগঙ্গাধর তীলকের ৬ বছরের কারাদণ্ড, সরদার অজিত সিংহ ও লালা রাজপুত রায়ের দীপান্তরের ফলে ক্রমশ স্বদেশী আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। সরকারের দমন নীতির কারনে বিপিন চন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের গ্রেপ্তার ও বিভিন্ন মেয়াদী সাজা প্রদান করা হয়। জনসভা ও সংবাদপত্রের ওপর বিধি-নিষেধ জারি করা হয়।
থমাস কার্লাইল এর সার্কুলার
বৃটিশ সরকার ছাত্র সমাজকে আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কার্লাইল সার্কুলার নামে একটি গোপন আদেশ জারি করে। থমাস কার্লাইল ছিলেন বাংলার প্রধান সচিব। এ সার্কুলারটি জারি করা হয় ১৯০৫ সালের ১৩ অক্টোবর। এ সার্কুলারের ফলে বাংলার শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা পেডলার সাহেবকে কোন কোন কলেজের ছাত্ররা পিকেটিং ও সংঘর্ষে জড়িয়ছিল তার লিস্ট দিতে বলেন।
জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনঃ
স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানকারী অনেক ছাত্র-শিক্ষক সরকারি দমননীতির কারনে স্কুল কলেজ ত্যাগ করেছিলেন। বহু ছাত্রকে স্কুল থেকে বহিষ্কারও করা হয়েছিল।
বঙ্গভঙ্গে মুসলমান ও পূর্ব বাংলার জনগনের প্রতিক্রিয়াঃ
১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা করলে হিন্দু জমিদারদের পাশাপাশি কতিপয় মুসলিম জমিদার ও আইনজীবী শ্রেনী বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করলেও সমগ্র বাংলা ও আসামের মুসলিম জনতা এ পরিকল্পনাকে স্বাগতম জানায়। কেননা নবগঠিত পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশে তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রসঙ্গত কারনে মুসলমান জনগন আশাবাদী হয়ে ওঠেন যে, নতুন প্রদেশে তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন ও স্বার্থ সংরক্ষন করতে সক্ষম হবেন। মুসলমান কৃষক সম্প্রদায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন এ কারনে যে, হিন্দু জমিদারদের নির্যাতন থেকে এবারে তারা রেহাই পাবেন। মুসলিম আইনজীবী, চিকিৎসক, বুদ্ধিজীবী ও বণিক সম্প্রদায় আনন্দিত হন এ জন্য যে এবারে তারা হিন্দু প্রতিপক্ষের প্রতিদ্বন্দিতা থেকে মুক্ত হবেন।
নতুন প্রদেশের পক্ষে মুসলমানগন কর্তৃক সম্পাদিত পত্রিকাগুলো এ পরিকল্পনাকে স্বাগত জানায় এবং এর সুফলগুলো জনসাধারনের জন্য তুলে ধরেন। মুসলমানদের সংগঠন মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি ও নবাব স্যার সলিমুল্লাহ কর্তৃক মুসলিম লীগ বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায় এবং এর পক্ষে প্রচারণা চালায়। এই সংকটকালীন মুহূর্তে বাংলার মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার জন্য নবাব সলিমুল্লাহ নিরলস পরিশ্রম চালিয়ে যান। টাঙ্গাইলের ধনবাড়ির জমিদার নবাব আলী চৌধুরী এবং শেরে বাংলা একে ফজলুল হক নবাব সলিমুল্লাহকে সহযোগিতা করেন। তারা বাংলার বিভিন্ন স্থানে সভা-সমাবেশ করে নতুন প্রদেশের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন এবং নবগঠিত প্রদেশের স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলেন।
বঙ্গভঙ্গ মুসলিমদের মনে এক প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। কিন্তু কলকাতার এক শ্রেণীর জমিদার ও ভূস্বামী বঙ্গভঙ্গ রদের পক্ষে ছিলেন।
বঙ্গভঙ্গ সময়কালীন মুসলমানদের ব্যর্থতাঃ
বঙ্গভঙ্গ করার পেছনে মুসলিম সমাজের খুব একটা ভূমিকা ছিল না। বঙ্গভঙ্গ করেছিলে বৃটিশ রাজ পরিবারের শাসনকার্যের সুবিধার্থে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ হওয়ার পরে মুসলিম সম্প্রদায় বুঝতে সক্ষম হন যে, বঙ্গভঙ্গ মুসলিম সম্পদ্রায়ের জন্য ভালো হবে। হিন্দুরা বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাংলা ভাষাভাষী সকলে অপকৌশল অবলম্বন করে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে করে সুযোগ নিয়েছে। কতিপয় মুসলিম নেতাও বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের ভূল ব্যাখ্যা বুঝেছে। ফলে মুসলমানগন তাদের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়। ফলে মুসলমানগন বঙ্গভঙ্গকে টিকিয়ে রাখতে পারে নি। হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের বিরুদ্ধে তেমন জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে নি। তাই মুসলমানদের দুর্বল নেতৃবৃন্দ্বর কারনে হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে সফলতা পেয়েছে।
বঙ্গভঙ্গ রদ ১৯১১ঃ
বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য হিন্দু সম্প্রদায় যে আন্দোলন পরিচালনা করে তা একসময় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে পরিচালিত হয়। বয়কট আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন ক্রমশ সন্ত্রাসবাদী রূপ নিলে সমগ্র বাংলা প্রদেশ ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলিম জড়িয়ে পড়ে। ফলে বহু মানুষ প্রাণ হারায়। তবুও বৃটিশ সরকার প্রথম দিকে তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। কঠোর হস্তে এ আন্দোলন দমন করতে থাকে। ফলে এ আন্দোলন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা, আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন অতি দ্রুত সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করলে বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন।
বৃটিশদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির কারনে মুসলমানদের বিশেষকরে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়। এদিকে ১৯১০ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ বড় লার্ট হয়ে আসেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ ক্ষমতালাভের পরপরই সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বাংলার সকল জেলার কংগ্রেস নেতা বঙ্গভঙ্গের জন্য তার নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন। তিনি হিন্দু নেতাদের ক্রমবর্ধমান উগ্র মনোভাব বুঝতে পেরে বঙ্গভঙ্গ রদের বিষয়ে সুপারিশপত্র বৃটিশ সরকারের নিকট পেশ করেন। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর পঞ্চম জর্জের অভিষেক অনুষ্ঠানে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেয়া হয়।
বঙ্গভঙ্গ রদের পর নতুন সিদ্ধান্তঃ
১) ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হয়। বৃটিশরা মনে করেন এতে কলকাতা যেমন সন্ত্রাসবাদের হাত থেকে রক্ষা পাবে। অন্যদিকে দিল্লীতে রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় মুসলিমরা কিছুটা খুশি হবেন।
২) মুসলমানগন বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্তে হতাশ হন। তারা তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন ঘটান। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে। উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলম বন্ধুত্বে চির ধরে। সাম্প্রদায়িকতারে মনোভাব চরম আকার ধারন করে।
সর্বশেষ উপর্যুক্ত আলোচনার সারমর্মে বলা যায়, একটি মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বঙ্গমাতাকে দ্বিখন্ডিত করার অজুহাতে কংগ্রেস তথা হিন্দু নেতাদের প্রবল প্রতিরোধের ফলে আন্দোলনের চাপে বৃটিশ সরকার তা রদ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ১৯৪৭ সালে সে কংগ্রেস এবং হিন্দু সমাজ অখন্ড স্বাধীন বাংলার পরিবর্তে বাংলা তথা বঙ্গমাতাকে দ্বিখণ্ডিত করনের প্রস্তাব দেয়। ১৯৪৭ সালে দ্বিতীয়বার বঙ্গভঙ্গ হয়।